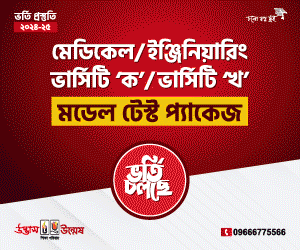ঈদের সারা দিন এবং পরদিন বাসি ঈদেও আত্মীয়স্বজনরা যেমন বাড়িতে আসতেন, তেমনি প্রতিবেশীরাও আসতেন। আবার প্রতিবেশীদের বাড়িতে আমরা খাবারও নিয়ে যেতাম। তখন ঢাকায় খুব গরিব মানুষ বা ভিখারি কমই ছিল। অনেক সময় কোরবানি ঈদের মাংস দেয়ার মতো পর্যাপ্ত ভিখারি পাওয়া না গেলে এতিমখানা বা মাদরাসায় কোরবানির মাংস পৌঁছে দেয়া হতো। কোরবানির পশুর চামড়া সব সময় মাদরাসা ও এতিমখানার জন্য বরাদ্দ ছিল।
আমার শৈশব বলতে ১৯৫০-এর দশক। ঢাকা তখন প্রাদেশিক রাজধানী, জমজমাট শহর শুধু বুড়িগঙ্গার তীর থেকে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন পর্যন্ত। এরপর গুলিস্তান সিনেমা হল, নির্মিয়মাণ ঢাকা স্টেডিয়াম, পুরানা পল্টন, সেগুন বাগিচা, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, শান্তিনগর, মালিবাগ, পরিবাগ, হাতিরপুল আর তেজগাঁওয়ে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট পাড়া। শাহবাগ হোটেল (এখনকার বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) তখন ঢাকার একমাত্র অভিজাত হোটেল সদ্য বানানো হয়েছে। সেখান থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দরের যে রাস্তা সেটাও গলির মতো, কারওয়ান বাজার, হলি ক্রস স্কুল আর মনিপুরি ফার্মের (ফার্মগেট) ভেতর গিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়েছে।
এখন যেখানে সোনারগাঁও হোটেল তখন সেখানে খাল ছিল। খালের উপর ছিল উঁচু একটা পুল। ’৫৩ খ্রিষ্টাব্দে এক বর্ষার দিনে সেই পুলের তলায় কাজের লোকদের কাঁধে চেপে এসেছিলাম মাছ ধরা দেখতে। অত ছোট বয়সে ঈদের কোনো স্মৃতি নেই।
বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। ওয়াইজ ঘাটের ৮ নং কুমারটুলিতে বিশাল আঙিনার ওপর বালিয়াটি জমিদারদের এক বাড়িতে ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল ইন্টালিজেন্স ব্যুরোর দপ্তর। বাবা সেখানে কাজ করতেন।
১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবাদের অফিস সেগুন বাগিচার নতুন ভবনে সরিয়ে নেয়ার পর কুমারটুলির বাড়িটা বাবা আর তাদের অফিসের অ্যাংলো সুপারিনটেন্ডেন্ট অগলি সাহেবকে বরাদ্দ করা হলো থাকার জন্য। তার আগে আমরা থাকতাম সূত্রাপুরে রূপলাল লেনের ছোট একটা দোতলা বাড়িতে।
বাবা আর তার বড় ভাই মাওলানা হাবিবউল্লাহ- অর্থাৎ আমার জ্যাঠা দেশভাগের আগে কলকাতায় একসঙ্গেই থাকতেন ওয়েলেসলি স্ট্রিটের কাছে ডক্টর্স লেনের দেবেন্দ্র ম্যানসনে। জ্যাঠা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক ছিলেন, পরে প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন।
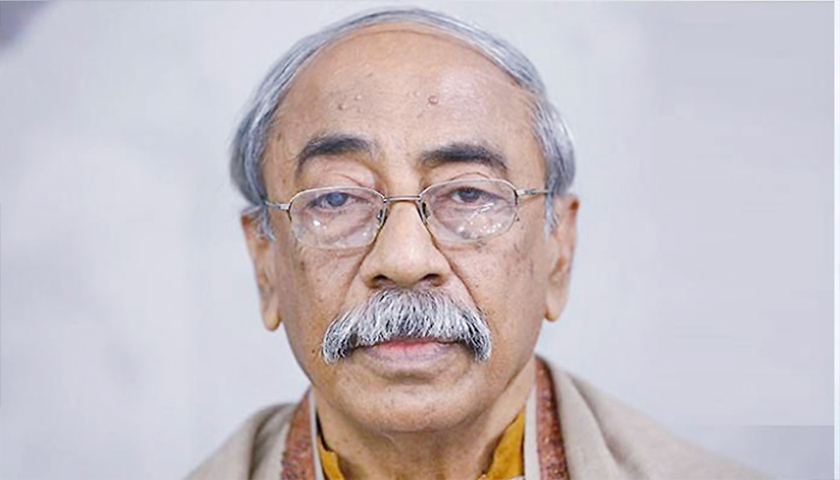
পার্টিশনের পর ঢাকায় এসে দুভাই একসঙ্গে থাকার মতো বড় বাড়ি পাচ্ছিলেন না। বাবা প্রথমে ইসলামপুরের নবরায় লেনের একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। বাবা মা আর আমরা তিন ভাই- আমাদের জন্য বাড়িটা বড় হলেও জেঠুর পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। জেঠতুতো ভাই পাঁচজন, বোন তিনজন; এ ছাড়া পোষ্য আত্মীয়-স্বজন মিলে বড় সংসার। ঢাকায় এসে জেঠু উঠেছিলেন মোঘলটুলিতে আলিয়া মাদ্রাসার হোস্টেলের কয়েকটা কামরায়। হোস্টেলের ছাত্রদের জন্য আলাদা গেট ছিল।
আমার আর ছোট ভাইর জন্ম হয়েছিল নবরায় লেনের বাড়িতে। ছোট ভাইর জন্মের পর মা অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় ডাক্তার বলেছিলেন তাকে গ্রামে মুক্ত বাতাসে থাকার জন্য। ইসলামপুর তখনও ঘিঞ্জি এলাকা। মার মামা হামিদুল হক চৌধুরী পাকিস্তানে জাঁদরেল রাজনীতিবিদ ছিলেন, একবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তেজগাঁওয় একশ বিঘা জমির ওপর তার একটা বাগানবাড়ি ছিল। তিনি থাকতেন টিকাটুলিতে। মার গ্রামে থাকার কথা শুনে তিনি বললেন, সেই বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকতে।
ইসলামপুর থেকে তেজগাঁওয়ের বাড়িতে এসেছিলাম ঘোড়ার গাড়িতে চেপে। ঢাকা তখন দুই ঘোড়ায় টানা পাল্কির মতো ঘোড়ার গাড়িতে বোঝাই ছিল। রিকশাও ছিল অনেক, তবে দূরে যেতে হলে ঘোড়ার গাড়িতে যেতাম। পাকা রাস্তার ওপর ঘোড়ার নাল বাঁধানো পায়ের খট খট শব্দ, চাকার ঘড় ঘড় শব্দ, ভেতরে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ, খড়খড়িওয়ালা জানালা তুলে বাইরের দোকানপাট আর ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে নবাবপুরের উঁচু পুল পেরিয়ে, ফুলবাড়িয়া রেলক্রসিং পেরিয়ে, গাছ গাছালিতে ঢাকা রমনার ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে দিয়ে, কারওয়ান বাজার হয়ে এক বিকেলে এসে নেমেছিলাম তেজগাঁওয়ের বাগানবাড়িতে।
এয়ারপোর্টে যাওয়ার পাকা রাস্তা থেকে বাঁয়ে কিছুটা কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে বাঁ হাতে ঢুকতে হয়েছিল বাগানবাড়ির সীমানায়। ভেতরে ঢুকে সুরকিবিছানো সরু রাস্তা ধরে কিছু দূর এগোলে ডানহাতে পুকুর। চওড়া বাঁধানো ঘাট, ঘাটের ওপরে হেলান দিয়ে বসার জায়গাও লাল সিমেন্টে বাঁধানো। তারপর উঁচু টিনের আটচালা বাংলো। দেয়াল আর মেঝে পাকা। চারদিকে চওড়া ঘেরা বারান্দা, সামনে পেছনে সিঁড়ি, পেছনের সিঁড়ির পাশে মস্ত বড় গন্ধরাজ ফুলের গাছ। গন্ধরাজের গাছ কখনও এত বড় হতে পারে আর কোথাও দেখিনি।
আমার আর ছোটভাইয়ের দেখাশোনা করত কোনো আয়া নয়, দশাসই চেহারার এক লোক। ওর নাম ভুলে গেছি, তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে, ওর হাতে ছয়টা আঙুল ছিল। আমাকে ও ডাকত ‘মাইজা মিয়া’, আর ছোটভাইকে ডাকত ‘কুট্টি মিয়া’। ছোটভাই বাবলুকে কোলে নিয়ে আমার হাত ধরে ও বাগানে ঘুরে বেড়াত, নানা রকম গাছ আর পাখি চেনাত। গাছভর্তি কামরাঙা, সফেদা, বিলিতি গাব, জামরুল এসব দেখে দিন কাটত। কখনও ও বৈঁচি ফল কুড়িয়ে আনত, তারপর মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিত। ক্ষুদে ক্ষুদে সেই বৈঁচি ফলের চমৎকার স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে।
বাগানজুড়ে ছিল বাদুড়ের ডানার ঝটপট শব্দ। ছয় আঙুলে ‘হুই, হুই’ বলে বাদুড় তাড়াত আর সকালবেলায় দুঃখ করত- পাকা ফলগুলো সব বাদুড়ে খেয়ে ফেলেছে। লিচুর সময় বাদুড়ের একটু অসুবিধে হতো। লিচুতে যখন রং ধরত, মালিরা সব গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিত। কোনো কোনো দিন জালে বাদুড় আটকে থাকত।
বাগানবাড়িতে ইলেকট্রিকের লাইন ছিল না। রাত হলে ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বালানো হতো, বারান্দায়ও হারিকেন ঝোলানো থাকত। বাবা আর ভাইয়ার ফিরতে ফিরতে প্রায়ই অন্ধকার হয়ে যেত। পাটুয়াটুলিতে ইন্সটিটিউট অব কমার্স নামে বাবা একটা সেক্রেটারিয়েল কোর্সের কলেজ খুলেছিলেন, কলকাতা থেকে ঢাকা আসার পরই। অফিস ছুটির পর তিন চারঘণ্টা সেখানে কাটাতেন তিনি। ভাইয়াও থাকত সঙ্গে। বাড়ি ফিরতে তাই রাত হতো।
অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে শুরু হতো ঝিঁঝি পোকার ডাক, তারপর ডাকত শেয়াল। গোটা বাগান বাড়িতে ছিল শেয়ালের ছড়াছড়ি। একটা ‘হুক্কা হুয়া’ ডাকল, আর অমনি চারদিক থেকে ‘হুয়া হুয়া, কেয়া হুয়া’ বলে অন্য শেয়ালরা কোরাসে গলা মেলাত। আমাদের ছয় আঙুলের তখন একমাত্র কাজ ছিল আমাকে গল্প শোনানো। কখনও বাবার ফিরতে যদি রাত বেশি হতো, মালিরা পুকুর ঘাটে বসে গল্প করত, বাড়ির চারপাশে ঘুরে টহল দিত আর মাকে বলত, ‘বিবি সাব, আমরা সজাগ আছি। ভয়ের কিছু নাই’। এই ছিল তখনকার ঢাকার তেজগাঁও এলাকা, যেটা এখন ঘিঞ্জি গ্রিন রোড।
আমার বয়স যখন ছয় তখন আমরা কুমারটুলির মস্ত জমিদার বাড়িতে উঠেছি। বাবা আর জেঠু আট বছর পর আবার একত্র হলেন। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন জেঠিমা। এগারো ভাইবোন ছাড়াও গ্রাম থেকে আত্মীয়রা আসতেন কারো চিকিৎসার জন্য, কেউ চাকরি খোঁজার জন্য, কেউ মামলা মোকদ্দমার কাজে, কেউ আবার বিদেশ যাবেন- পাসপোর্ট ভিসা করে প্লেনে ওঠার জন্য। সারা বছরই বাড়িটা গম গম করত।
দুই
কুমারটুলি বাড়ির ঈদের স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করে চোখে ভাসে। আট দশ রোজা না যেতেই ঈদের প্রস্তুতি আরম্ভ হতো। কুমারটুলির বাড়িতে ঈদে ভাই-বোনরা কেউ তৈরি জামা কাপড় পরিনি। বাবা আর জ্যাঠা পাটুয়াটুলির দোকান থেকে কাপড়ের থান কিনে আনতেন। তখন গোটা ঢাকা শহরের সবচেয়ে অভিজাত কাপড়ের দোকান সব পাটুয়াটুলিতে। ওয়াইজ ঘাটের মোড় থেকে সদরঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে অনেক কাপড়ের দোকান। সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিল ফেব্রিক হাউস আর সিল্ক প্যারাডাইস। শাড়ির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয় আর অমৃত বস্ত্রালয়। সদরঘাটের মোড়ে ছিল বাটার জুতোর দোকান। রেডিমেড কাপড়ের দোকানও ছিল বেশ কয়েকটা, ঈদ ছাড়া অন্য সময়ে যেখান থেকে আমাদের প্যান্ট শার্ট কেনা হতো।
ঈদের অনেক আগেই ছেলেদের পাঞ্জাবির জন্য আনা হতো সাদা আদ্দির কাপড়ের থান আর পায়জামার জন্য সুতির লং ক্লথ। বোনদের সালোয়ার কামিজের জন্য আনা হতো সিল্কের থান। সিল্কের ভেতর সবচেয়ে দামি ছিল লেডি হ্যামিল্টন। বোনেরা দামি সিল্ক পরলেও সবার ড্রেস বানানো হতো একই থান থেকে।
বড়দির তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে, দুলাভাই ও বাচ্চাকাচ্চাসুদ্ধ আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। বড়দি শাড়ি পরতেন। মেজদি ছোড়দি এবং ঈদের সময় অন্য কোনো জ্ঞাতি বোন যদি থাকতেন সবার পোশাকের বরাদ্দ একই প্রিন্টের সিল্ক। বাড়িতে দর্জি এসে কাপড়ের মাপ নিয়ে যেত। ঢাকার দর্জিদের বলা হতো খলিফা, কী কারণে জানি না, ঢাকা বিশারদ বন্ধু মুনতাসীর মামুন হয়তো বলতে পারবেন। ইসলামপুরে অনেক টেইলরিং শপ বা দর্জির দোকান ছিল।
বোনেরা একই থানের পোশাক পরলেও খবরের কাগজ থেকে বোম্বাই ছবির নায়িকাদের পোশাকের ছবি তারা কেটে জমাতেন। তাদের সালোয়ার কামিজের ছাঁটে বৈচিত্র্য থাকলেও ছোট বড় নির্বিশেষে পরিবারের সব পুরুষের আদ্দির পাঞ্জাবি আর লং ক্লথের পায়জামা। তবে এতে করে ঈদের আনন্দে এতটুকু ঘাটতি ছিল না। ঈদের দিন নতুন পোশাক পরার মজাই ছিল অন্যরকম।
বোনেরা অবশ্য ভাইদের দুর্দশা দেখে ঈদের সময় রুমাল উপহার দিতেন। দর্জিকে বলা থাকত পাঞ্জাবির কাপড় থেকে টুকরো যা বাঁচবে সেগুলো ফেরত দিতে হবে। আদ্দির কাপড়ে কুরুশকাঁটা দিয়ে সিল্কের সুতোর বর্ডার বানিয়ে কখনও এক কোণে এম্ব্রয়ডারি করে ফুল তুলতেন। ঈদের দিন বাবা আর জেঠু এই রুমালেই আতর মাখিয়ে দিতেন। হাতের কবজি আর কানের গোড়ায়ও আতর দেয়া হতো। ইসলামপুরে কাশ্মিরীদের বড় আতরের দোকান ছিল। রাস্তা পর্যন্ত আতরের সুগন্ধ ছড়াত।
আমরা ছোটরা ছবি এঁকে ঈদ কার্ড বানিয়ে একে অপরকে উপহার দিতাম। কখনও বন্ধুদেরও ডাকে পাঠাতাম। ডাকে বন্ধুদের ঈদ কার্ড পাঠানোর অভ্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবধি ছিল। বড় হওয়ার পর স্টেশনারি দোকান থেকে নানা রঙের বাহারি ঈদ কার্ড কিনতাম। অন্তর্জালে আচ্ছন্ন এখনকার শিশু-কিশোরেরা জানে না ডাকে ঈদ কার্ড পাওয়া কী আনন্দের!
ছোটবেলায় দেখেছি শাড়ি কেনার জন্য মা জেঠিমারা কখনও দোকানে যেতেন না। দোকানের কর্মচারী ফরমায়েশ মতো পঁচিশ তিরিশটা শাড়ি আনতেন চাদরে বেঁধে। সেখান থেকে বড়রা শাড়ি বাছতেন। ফেরিওয়ালারা ‘চাই ঢাকাই শাড়ি’ বলে জামদানি শাড়ি ফেরি করত। কাচের চুড়ি আর নকল গয়নাও কেনা হতো ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে। এ নিয়ে আমাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। তবে বাবার সঙ্গে যখন সদরঘাটে বাটার দোকানে স্যান্ডেল কিনতে যেতাম তখন আনন্দ আর উত্তেজনার কোনো সীমা ছিল না।
পোশাকের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হতো ভোজনের পর্ব। ঈদের প্রধান পদ সেমাই যদিও দোকানে কিনতে পাওয়া যেত কিন্তু আমাদের বাড়িতে ঈদের সময় দোকানের সেমাই কেনা হতো না। ওতে নাকি মেশিন মেশিন গন্ধ থাকে। সেমাই বানানো হতো বাড়িতে। তখন মধ্যবিত্ত সব পরিবারেই সেমাই বানাবার ছোট পেতলের মেশিন থাকত। ময়দা ভালোমতো মেখে নরম করে মেশিনের ভেতর ঠেসে দেয়া হতো।
তারপর হাতল ঘোরালে নিচ দিয়ে সেমাই বেরিয়ে আসত। নিচে ছাঁচ লাগানো থাকত সরু আর মোটা সেমাইয়ের জন্য। সেই সেমাই রোদে শুকিয়ে কাচবাঁধানো টিনের বাক্সে তুলে রাখা হতো ঈদের দিন রান্নার জন্য। আট দশ বছর বয়সে ছোট সেমাই মেশিনে হাতল ঘোরানোর কথা এখনও মনে আছে।
সেমাই ছাড়া ঈদের দিনের জন্য ‘সেউই’ পিঠাও বানানো হতো আট দশ দিন আগে। ময়দার বদলে চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠার ময়ান বানানো হতো। সরু চালের মতো সেউই পিঠা বানানো মেয়েদের একচেটিয়া ছিল। আগেকার দিনে মেয়েদের অন্যতম গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো পিঠা বানানোর ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতাকে। বাবাদের কাছে শুনেছি তাদের ছোটবেলায় গ্রামে সেমাই-এর প্রচলন ছিল না। নানা রকম পিঠা দিয়ে সকালে ঈদের আপ্যায়ন হতো।
ঈদ যত ঘনিয়ে আসত ছোটদের আনন্দ আর উত্তেজনার সীমা থাকত না। ঢাকার আদি বাসিন্দাদের দেখেছি চাঁদ দেখার পর থেকেই সাড়ম্বরে ঈদের উৎসব শুরু করতে। ঈদের আগের রাতকে তারা বলেন ‘চান রাইত’, অর্থাৎ চাঁদ দেখার রাত। রোজার মাসে যারা পাড়ায় পাড়ায় কাসিদা গাইতেন তারা ‘চান রাইতে’ কাওয়ালির মাহফিল বসাতেন বিভিন্ন পার্কে। ঢাকায় তখন প্রত্যেক মহল্লায় খেলার মাঠ বা পার্ক ছিল।
আমাদের চেয়ে বড় যারা তাদের সবচেয়ে আনন্দ ছিল ঈদের নতুন সিনেমা দেখায়। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল মায়া সিনেমা, ষাটের দশকে মালিক বদল হয়ে যার নাম হয়েছিল স্টার সিনেমা। স্টারের ঠিক সামনে ছিল মুন সিনেমা। সদরঘাটে ছিল রূপমহল সিনেমা। ভিক্টোরিয়া পার্কের (পরে বাহাদুর শাহ পার্ক) পর মুকুল সিনেমা (পরে নাম হয়েছে আজাদ সিনেমা)। ওয়াইজ ঘাট থেকে বাঁয়ে ইসলামপুর গেলে লায়ন সিনেমা, নয়া বাজারে নাগর মহল, আরেকটু আগে বংশালে মানসী সিনেমা।
অন্যদিকে আর্মানিটোলায় শাবিস্তান, মৌলবিবাজারে প্যারাডাইস সিনেমা। ফুলবাড়িয়া স্টেশন পার হলে গুলিস্তান, নাজ আর বৃটানিয়া সিনেমা। বলাকা আর মধুমিতা হয়েছে ষাটের দশকে। এক দেড় মাইলের ভেতর এক ডজনের ওপরে সিনেমা হল। হলে হলে ঈদে নতুন ছবি। পাকিস্তানি ছবি একটা বা দুটো। বাকি সব হলে ভারতীয় ছবি। ষাটের দশক থেকে শুরু হয়েছে ঈদের সময় ঢাকার ছবি মুক্তি দেয়া। গুলিস্তান আর নাজে বাংলা বা উর্দু ছবি কমই দেখানো হতো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ দুটো অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ ছিল হলিউডের ছবির জন্য বিখ্যাত।
স্টার সিনেমায় রাতে যখন শো চলত তখন আমাদের বাড়ি থেকে ছবির গান, কখনও সংলাপও শোনা যেত। হলের সামনে গাড়ি রাখার জায়গা ছিল না। হল মালিকদের দু-তিনটা গাড়ি আমাদের বাড়িতে পার্কিং করত। বিনিময়ে প্রতি মাসে নতুন ছবির জন্য দশ বারোটা ফ্রি পাস আমাদের জন্য বরাদ্দ ছিল ওপরের ক্লাসে। গেট কিপাররা ছোটদেরও চিনত। ছুটির দিনে কখনও হলের সামনে ঘুর ঘুর করতে দেখলে ডেকে ভেতরের ফাঁকা সিটে বসিয়ে দিত। তবে হাউসফুল হলে পাস ব্যবহার করা যেত না।
ঈদের দিন ঘুম থেকে উঠতাম ফজরের আজানের সময়। কুমারটুলির বাড়িতে রান্নাঘর ছিল মূল বাড়ি থেকে দূরে, আগে যেখানে জমিদারদের চাকর গাড়োয়ান, পেয়াদারা থাকত। তার সামনেই শানবাঁধানো কুয়োতলা। কাজের লোক বালতিতে করে পানি তুলে দিত। তাতেই ছোটরা হুল্লোড় করে গোসল সেরে বাড়িতে ছুটতাম নতুন কাপড় পরার জন্য। এরপর ছিল ঈদের দিনের সবচেয়ে আনন্দঘন সময়। নতুন কাপড় পরে বড়দের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার ধুম। সালামের বিনিময়ে ঈদের সালামি ছিল এক টাকার কড়কড়ে নোট। বাবা, জেঠু, জেঠিমা ছাড়া বড় ভাইবোনরা গোটা টাকা দিতেন বলে মনে পড়ছে না।
শুধু বড়দা শহীদুল্লা কায়সার জেলে না থেকে বাড়িতে থাকলে এক টাকা সালামি দিতেন। বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়রা বেড়াতে এলে তাদেরও সালাম করতাম সালামি পাওয়ার আশায়। কখনও পেতাম, কখনও পেতাম না। দিনের শেষে হিসাব করতাম কে কত সেলামি পেয়েছে, সেলামির টাকায় কী কী কেনা হবে? সেলামির পর সবচেয়ে আনন্দের ছিল নামাজে যাওয়া আর নামাজের পর কোলাকুলি। সবাই জায়নামাজ নিয়ে ঈদের নামাজে যেতাম। নামাজের পরই ছিল কোলাকুলির পালা। বড়রা ছোটদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে কার্পণ্য করতেন না।
রোজার ঈদে নামাজে যাওয়ার আগে সেমাই বা পায়েস মুখে দেয়ার রেওয়াজ থাকলেও কোরবানি ঈদের সময় গরু-খাসি জবাইয়ের আগে পর্যন্ত বড়রা নাশতা খেতেন না। ঈদের নাশতা যে কত পদের হতো বলে শেষ করা যাবে না। রান্না শুরু হতো আগের দিন থেকে। গরুর গোশত রান্না হতো দুদিন আগে। ঈদের দিন দুপুর পর্যন্ত রান্না ঘরে চুলো জ্বলত। সকালের নাশতার পরই শুরু হতো দুপুরের পোলাও, কোর্মা, রেজালা, কাবাব, কোফতা রান্না। রাতে হতো বিরানি আর রোস্ট। বিরানির সঙ্গে বোরহানি অপরিহার্য। আমাদের ঢাকাইয়া বাবুর্চি রশিদের বোরহানির স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে।
১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জেঠু কায়েতটুলিতে বাড়ি কিনে কুমারটুলির বাড়ি থেকে চলে যান। তখন থেকে আমাদের পরিবারে একথানের কাপড় দিয়ে ঈদের পোশাক বানানোর সমাপ্তি ঘটেছিল। বাবা নতুন পোশাক কিনে দিতেন। জেঠিমাও দিতেন। বাড়ি আলাদা হলেও ঈদের দিন নামাজ পড়েই বাবার সঙ্গে রিকশায় করে আমি আর ছোট ভাই বাবলু কায়েতটুলি চলে যেতাম। দুপুরে খেয়েদেয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরতাম। এরপর বড় ভাই যেতেন- ছোড়দা, বাহার ভাই, সাবধন ভাই, ছোড়দি, মেজদিদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে।
১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে ‘মোঘল-এ আযম’ মুক্তি পাওয়ার পর ভাইয়া আর ছোড়দারা ঈদের ছুটিতে দল বেঁধে কলকাতা গিয়েছিলেন সর্বকালের আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ছবিটি দেখার জন্য। ক্লাস টেনে ওঠার পর আমি পরিবারের সদস্যদের বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে কিংবা একা ছবি দেখা আরম্ভ করেছি। এর আগে হাতে গোনা যে কটা ছবি দেখেছি কখনও বাবা বা ভাইয়ার সঙ্গে কিংবা কুমারটুলির বাড়িতে থাকতে বড়দি, মেজদি, ছোড়দিদের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর মেজদা জহির রায়হানের সঙ্গে ফিল্ম সোসাইটির ছবি দেখতে যেতাম। মেজদা বলে রেখেছিলেন, ফিল্ম সোসাইটি যখন কোনো ভালো ছবি দেখাবে আমি যেন তাকে নিয়ে যাই।
ছোটবেলায় ঈদের সময় স্কুলের লম্বা ছুটিও কম আনন্দের ছিল না। আমাদের মিশনারি স্কুলে সব ধর্মের উৎসবে সব ধর্মের ছাত্র-শিক্ষকের অংশগ্রহণ স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। ক্লাস নাইনের মুসলিম ছাত্ররা স্কুলের টাকায় বড় মিলনায়তন ভাড়া করে ঈদে মিলাদুন্নবিতে মিলাদের আয়োজন করত। হাজার খানেক ছাত্র-শিক্ষককে জায়গা দেয়ার মতো বড় মিলনায়তন স্কুলে ছিল না। তবে হিন্দু ছাত্ররা স্কুলের মাঠে সরস্বতী পূজার আয়োজন করত। খ্রিস্টান ছাত্ররা বড়দিনে কেক কাটত। ঈদ, পূজা বা বড়দিনের মিষ্টির বাক্সে সবার সমান অধিকার ছিল।
১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগে কে হিন্দু কে মুসলমান এ নিয়ে এতটুকু প্রশ্ন আমাদের ভেতর ছিল না। হিন্দু বন্ধুরা যেমন ঈদের দিনে বেড়াতে আসত, পূজোর সময় তাদের বাড়ি যাওয়াও অবধারিত ছিল।
ঈদের দিন আমাদের গৃহশিক্ষক ছাড়াও স্কুলের কোনো কোনো শিক্ষক বিকেলের দিকে বেড়াতে আসতেন। স্কাউট টিচার নিকোলাস স্যারের প্রিয় ছাত্র হওয়ায় আমাদের কুমারটুলির বাড়িতে তিনি কয়েক বারই এসেছিলেন। স্কাউটিং করার সুবাদে আমরা তিন ভাই-ই তার প্রিয় ছাত্র ছিলাম।
রোজার ঈদকে কেন ছোট ঈদ বলা হয় আমি জানি না। কোরবানি ঈদ তিন দিন ধরে হলেও ছোটবেলায় রোজার ঈদেই বেশি আনন্দ ছিল। পুরনো ঢাকায় সেকালে ঈদের মেলা বসত চকবাজার আর বংশালে। কোরবানি ঈদের সময় বাবাদের সঙ্গে বংশাল যেতাম গরু কেনার জন্য।
মনে আছে কুমারটুলির বাড়িতে আমাদের যৌথ পরিবারে প্রথম গরু কেনা হলো ষাট টাকা দিয়ে, যেটা এখন ষাট থেকে সত্তর হাজারের কম হবে না। পরের বছর একই আকারের গরু কেনা হলো আশি টাকা দিয়ে। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সে কী আক্ষেপ! এ বছরে গরুর দাম কুড়ি টাকা বেড়ে গেছে, দেশে হচ্ছেটা কী? হ্যাঁ, এর পরের বছরই পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়েছিল। কুমারটুলির বাড়ি থেকে বড়দাকে আবার গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হলো। পরের ঈদের মেজদা আর ছোড়দা বড়দার জন্য খাবার নিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেন। (ঈষৎ সংক্ষেপিত)