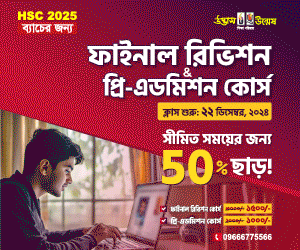শঙ্খ ঘোষের ‘হামাগুড়ি’ কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়েই শুরু হোক আলোচনা! আজকের বাংলাদেশের পরিস্থিতি যেনো অনেকটাই বলে দেয় কবিতাটি।
“ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ। বাইরে কি ঝড় হচ্ছে?
...
'কিছু কি খুঁজছেন আপনি?'
শুনতে পাচ্ছি, 'খুঁজছি ঠিকই, খুঁজতে তো হবেই
পেলেই বেরিয়ে যাব, নিজে নিজে হেঁটে।'
'কি খুঁজছেন?'
মিহি স্বরে বললেন তিনি ‘মেরুদণ্ডখানা।’
সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলকালো ফের। চমকে উঠে দেখি........
একা নয়, বহু বহু জন
একই খোঁজে হামা দিচ্ছে এ-কোণে ও কোণে ঘর জুড়ে।”
সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। একটি পরাধীন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মতো তামাশা আর কিছু হতে পারে না। কারণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত হলো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং তার স্বাধীন ও সার্বভৌম চেতনাসম্পন্ন নাগরিক। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে যা ঘটছে, তাতে এটি স্পষ্ট যে, আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের কাছে বন্ধক দিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা রক্ষা করতে চাইছি। আমাদের মনে রাখা দরকার, যখন বিষয়টি স্বাধীনতার তখনকার রাজনৈতিক তৎপরতার স্বরূপ, আর যখন বিষয়টি শাসনতান্ত্রিক অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চার তখনকার রাজনৈতিক তৎপরতার স্বরূপ ভিন্ন।
১৭ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি ও তার সমমনারা মনে করছে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার অগণতান্ত্রিক, জোর করে ক্ষমতায় আছে এবং এই সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকলে আগামী নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের পক্ষে রাখতে নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন সরকার অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে দেবে না। তাই যারা ক্ষমতায় যেতে চান তাঁরা একজোট হয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার দাবি জানাচ্ছেন। এটি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট। যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মীমাংসা করবে। অথচ রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাথে নিয়ে বিবাদমান রাজনৈতিক দলগুলো এই সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। তারা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর হস্তক্ষেপ কামনা করছে। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রিটেন, চীন ও ভারত রয়েছে। আর এই প্রত্যাশার মধ্যেই একজন নাগরিকের কিংবা একটি রাজনৈতিক দলের সার্বভৌম চেতনার বিসর্জন ঘটে।
তবে এবার যা ঘটছে তা খুব যে নতুন, তা বলা যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতরা ২০০৬ থেকে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ‘গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার জন্য কি মেহনতই না করেছেন! তার আগেও এমন নজির মেলে। আমাদের সাংবাদিকরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন দেশ কি কি করতে পারে বা ভাবছে, তা জানতে নির্দ্বিধায় তাদের কাছে দিনের পর দিন ধর্ণা দিয়েছেন, দিয়ে যাচ্ছেন। সেখান থেকে পাওয়া ‘অমিয় সুধা’ সংবাদ আকারে অত্যন্ত গুরুত্ব ও তমিজের সাথে পরিবেশিত হচ্ছে পত্রিকার পাতায় ও টিভি চ্যানেলগুলোতে।
আলোচনাটা খুব জটিল কিছু নয় এবং বিষয় হিসেবেও অনেক পুরনো। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট সমাজ বিষয়টি বহু আগেই সুরাহা করেছে, যা আমরা এখনো পারিনি। যে কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে সর্বশেষ নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে এবং তাঁর পক্ষে মার্কিন নাগরিকেরা সহিংস বিক্ষোভে যোগ দিলেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতিনিধিদের কোনো বক্তব্য থাকে না।
আমরা যারা ‘স্বাধীন’ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি, বেড়ে উঠেছি এই জেনে যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। অন্যান্য মৌলিক শর্তের পাশাপাশি একটি রাষ্ট্রে যখন প্রতিটি ‘সুস্থ’ নাগরিক স্বাধীনভাবে বা নিজের ক্ষমতায় তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তখন ওই রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলা যায়। বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয় রাজনৈতিক দল বা জোটকে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী তারা জনগণের সমস্যাবলী সমাধানের নানাবিধ প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়, ভোটারদের কাছে ভোট চায়। এই চর্চা একটি রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যখন ওই রাষ্ট্রের কোনো ‘ক্ষমতাবান ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল’ দ্বারা ব্যাহত হয়, তখন তা অগণতান্ত্রিক চর্চা নামে অভিহিত হয়। তখন গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তিগুলোর কাজ হলো- অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এ কাজ হচ্ছে বল প্রয়োগ, যা কোনো মান-মাত্রা দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। এই ক্ষেত্রে ওই রাষ্ট্রকে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী দেশীয় রাজনৈতিক শক্তি বা দলগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় যখন অন্য কোনো রাষ্ট্র বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি প্রভাব নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে, তখন বুঝে নিতে হয়, ওই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বেহাত হয়ে গেছে।
ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা যায়। সময়টা ১৯৪১। অক্ষ শক্তির জার্মান বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানিজ বাহিনী মার্কিন ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে ইউরোপের যুদ্ধ পৃথিবীতে আরও ছড়িয়ে পড়ে। জাপান বার্মা দখল করে। বঙ্গোপসাগরে জাপানি যুদ্ধ জাহাজের আনাগোনা। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপও দখল করেছে। যে কোনো সময় পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে ভারতবর্ষের মূল ভূ-খণ্ডে অভিযান শুরু করবে জাপান, এমন এক পরিস্থিতি। প্রশ্নটা উঠলো, এটা ভারতবাসীর সমস্যা কি না? জাপান ভারত আক্রমণ করে দখল করে নিলে শাসক হিসেবে ব্রিটিশদের জায়গায় জাপান আবির্ভূত হবে। অর্থাৎ, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা হারাবার বিষয় নেই। তাই যখন ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটেন চাচ্ছিলো ভারতবাসী তাদের জনবল ও সম্পদ নিয়ে মিত্র শক্তির হয়ে অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিক, তখন এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্নটি যথাস্থানে তুলে ধরেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁর বক্তব্য ছিলো এ রকম, একটি পরাধীন জাতি এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আজ ভারত যদি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হতো, তা হলে একটি গণভোটের মধ্য দিয়ে যুদ্ধে যোগদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। একটি পরাধীন দেশের মানুষ কেনো এক আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক শাসকের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবে? যদিও মওলানা আজাদের এই স্বাভাবিক চিন্তা বা যুক্তিবোধ তাড়িত রাজনৈতিক অবস্থান মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুসারিদের অহিংসার আন্দোলন থেকে তেমন টলাতে পারেনি এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের জনবল ও সম্পদ ওই যুদ্ধে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উপায়ে ব্যবহার করেছে। পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা যেভাবে এগিয়েছে, তাতে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে এটি দাবি করা যায় না, বরং এটাই বলা হয়, ব্রিটিশ শাসক ভারতীয় রাজনীতিকদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর করে গেছে। তবে ঘটনা পরম্পরায় মওলানা আজাদের সেই যৌক্তিক অবস্থানের প্রভাব থাক বা না থাক, তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টিকে জনগণের সার্বভৌম সত্ত্বার সাথে শর্তাধীন করেছিলেন, সেটি রাষ্ট্র, শাসন ব্যবস্থা, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনায় আজো প্রাসঙ্গিক। এমনকি যুক্তির বিচারে মওলানা আজাদের অবস্থানটিই যে পরাধীন ভারতবাসীর জন্য মর্যাদাকর ও তার স্বাধীনতার প্রশ্নে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারতো, সেটি অনেকাংশে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং স্বীকার করে গেছেন।
‘সার্বভৌম চেতনা’র জন্য চাই রাজনৈতিক সচেতনতা, যা আর্থ-সামাজিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। আমাদের সমাজ রয়েছে। সেখানে মানুষ অসংখ্য আর্থ-সামাজিক কর্ম-তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন বেঁচে থাকার তাগিদে, আরেকটু ভালো থাকার আশায়। কিন্তু বড় মুশকিল হয়ে গেছে, এই সার্বভৌম চেতনা বিষয়টি বিশেষ জ্ঞানভুক্ত হয়ে ‘গবেষণাগারে’ ঢুকে গেছে। ওই বোধের আকার-প্রকার আমাদের সাধারণের (হেজেমনি তৈরি করতে পারে না যারা) নাগালের বাইরে। আর যাঁরা বিষয়টি বোঝেন, তাঁদের স্বার্থগত অবস্থান সাধারণের স্বার্থের থেকে ভিন্ন, ক্ষেত্র বিশেষ বিরোধপূর্ণ। অর্থাৎ, এসব বিজ্ঞজনের জীবন-জীবিকা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সাধারণের জীবন-জীবিকার উন্নয়নের সাথে সমান্তরাল ও একমুখি নয়। হয়তো সে কারণেই এসব ‘বিশেষ জ্ঞান’ সামাজিক জ্ঞানে রূপান্তরের চেষ্টা তেমন একটা দেখা যায় না। নিঃসন্দেহে বিরাজমান এই পরিস্থিতির সুবিধা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো পাচ্ছে। ফলে তারাও জনমনে সার্বভৌমত্বের ধারণা যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে বিষয়ে বেশ সচেতন।