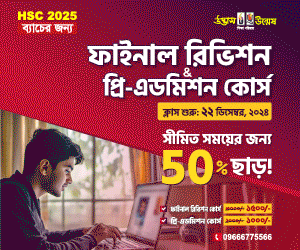শিক্ষার মান বাড়ছে কি? মান বৃদ্ধির প্রচারিত নিরিখটি হচ্ছে নম্বর ও গ্রেড। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরপরই নকলের এক মহোৎসব দেখা দিয়েছিল। এখন সেটা নেই। এখন আর নকলের দরকার পড়ে না; শিক্ষার্থীদের উচ্চ নম্বরের সিঁড়ি ভাঙাতে সহায়তাদানের জন্য কোচিং সেন্টার আছে, রয়েছে গাইড বুক, আছে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি। দেখা দিয়েছে সরকারি উদারতা। সরকার পরীক্ষকদের উদার হতে উদ্বুদ্ধ করছে, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রসন্ন হয়, নকল করাটা অনাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং সরকার ও দেশের সুনাম বৃদ্ধি পায়। সব মিলিয়ে এটি একটি ভয়াবহ আত্মপ্রতারণা। প্রতারণাটা যে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া শুরু হয়ে গেছে। আগামীতে আরও ভয়াবহভাবে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দেশ রূপান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ তথ্য জানা যায়। নিবন্ধটি লিখেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

নিবন্ধে আরো জানা যায়, ঔপনিবেশিক ইংরেজ-আগমনের আগে আমাদের দেশে শিক্ষা ছিল শিক্ষানির্ভর, পরে হয়ে দাঁড়াল পরীক্ষানির্ভর। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে; প্রাথমিক লক্ষ্যটা শিক্ষাদান ছিল না, ছিল পরীক্ষা গ্রহণ। প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়পত্র দিত, শিক্ষার্থীরা পড়ত কলেজে গিয়ে। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিএ পরীক্ষা নেওয়া হয়; পরীক্ষার্থী ছিলেন দশজন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দশজনের ভেতর কেউই পাস করতে পারেননি; এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও নন। পরে বিশেষ বিবেচনায় সাত নম্বর গ্রেস দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও অপর একজনকে পাস করিয়ে দেওয়া হয়। গ্রেস মানে করুণা। তখন ছিল বিদেশি কৃপণের করুণা, এখন এসেছে স্বদেশি দিলদরিয়াদের বদান্যতা; ওটি যদি খরা হয়, এটি তবে প্লাবন; বলাবাহুল্য শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও দেশবাসীর জন্য এই দুই চরমের কোনোটিই কাক্সিক্ষত নয়। কাক্সিক্ষত হলো স্বাভাবিক প্রবাহ, যেটি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমনই কপাল।
জ্ঞানার্জন নয়, পরীক্ষায় সাফল্যই ছিল মুখ্য বিবেচনা। এমনকি বিএ প্লাকড হওয়াও সম্মান বহন করত, বোঝা যেত যে ব্যক্তিটি বিএ পরীক্ষার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল। এখনো যা চলছে তা হলো ভালো ফল করার জন্য উন্মত্ত প্রচেষ্টা। প্রাইভেট পড়া ও পড়ানো আগেও ছিল, কিন্তু তাতে একটা সঙ্কোচ থাকত, যে শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়ছে তার মেধা সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিত, এখন ওসব নেই, প্রাইভেটে এখন লজ্জা শরমের বালাই নেই, সে এখন একেবারেই পাবলিক। বাজারের মতো উন্মুক্ত। পরীক্ষা যে মেধা যাচাইয়ের প্রকৃষ্টপন্থা নয়, তার বহু প্রমাণ আছে; শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আনুষ্ঠানিক পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্রের অকৃতকার্যকারিতা।
শিক্ষাব্যবস্থার নিজের ভেতরকার ত্রুটি কেবল পরীক্ষাকেন্দ্রিকতার ভেতর নয়, পরীক্ষার ধরনের মধ্যেও বিদ্যমান। পরীক্ষা করা হয় পরীক্ষককে ফাঁকি দিয়ে নম্বর সংগ্রহের দক্ষতার, পরীক্ষা নেওয়া হয় না শিক্ষার্থীর প্রকৃত মেধার এবং তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনের, এক কথায় তার মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের শিক্ষার। শিক্ষা সংস্কারের নানা রকমের উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, মূল ব্যাপারটা পরিণত হয়েছে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারে। যেমন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা বলে একটি বস্তুকে আনা হয়েছে, সেটির চরিত্র শিক্ষার্থীরা বুঝবে কী, শিক্ষকরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি, ফলে অগতির সেই পুরনো গতি গাইড বুকের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় থাকছে না। আবার একেবারে প্রাথমিক স্তরেই নতুন করে একটি পাবলিক পরীক্ষা চাপানো হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানান্বেষণকে সরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে আতঙ্ক এবং পরীক্ষার প্রস্তুতির নামে ছল-জোচ্্চুরিসহ মনোযোগ ও সময় নষ্ট করার তৎপরতায় দক্ষতা অর্জন শৈশব থেকেই শুরু হয়ে যাবে। পরবর্তী সময় ওই পথ ধরেই সে এগোবে, যতটা এগোতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে সবাই আসে না এবং যারা আসে তাদের অনেকেই অকালে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়ারা অর্ধশিক্ষিত রয়ে যায়। আর যারা মুখস্থ করে পাস করতে থাকে তারাও অর্ধশিক্ষিতই। অর্ধশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই অশিক্ষার চেয়েও ক্ষতিকর। আবার প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেখানে মেধাবান শিক্ষকরা যায় না; প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থাকে অবহেলিত, ফলে ভিত্তিটা দুর্বলই রয়ে যায়। শিক্ষা পদ্ধতিতে যেসব পরিবর্তন নানা হয় সে বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মতামত নেওয়ার কোনো নজির নেই। ধরা যাক ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারটা। ইংরেজি এক সময়ে ছিল বিদেশি ভাষা, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় ভাষা। কোন পদ্ধতিতে এই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কিন্তু তাতে করে শিক্ষার মান যে বেড়েছে তা মোটেই নয়। প্রচলিত পদ্ধতি ছিল গ্রামার, ট্রান্সলেশন ও সাহিত্যনির্ভর। সেটা ছিল বেশ উপযোগী। শিক্ষকরা ওই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। অভিভাবকরাও ওটাকে জানতেন। পরিবর্তন করে সেখানে আনা হয়েছে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ। যেখানে গ্রামার, ট্রান্সলেশন ও সাহিত্য কিছুই নেই। ধারণা করা হয় যে, এই পরিবর্তন একটা কারণ যার দরুন ইংরেজি শেখার ব্যাপারে আমাদের শিক্ষার্থীরা সুবিধা করে উঠতে পারছে না। আরও চমৎকার খবর এসেছে। সেটা হলো এখন থেকে লিসনিং ও স্পিকিংকে গুরুত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে ওই দুই দক্ষতার জন্য দশ দশ করে বিশ নম্বর বরাদ্দ রাখা হবে। প্রশ্ন হলো কে বলবে, কে শুনবে? ইংরেজি শিক্ষাটা কি জন্য দরকার? সেটা কি গোটা জাতিকে দ্বিভাষিক করে তোলার জন্য? তা ছাড়া যারা বাংলাই ভালো করে বলতে পারে না তারা কেন ইংরেজি শুনতে ও বলতে শিখবে? প্রয়োজন যা তা হলো পড়ার ও লেখার শক্তি। শিক্ষার্থী যাতে ইংরেজিতে লিখিত বইপত্র পড়তে ও বুঝতে পারে এবং নিজেকে ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে তার নিশ্চয়তা প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য যে, লিখতে পারবে সে বলতেও পারবে। তার ব্যবস্থা না করে শোনা ও বলার ওপর এই অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়াটা একটা নতুন অপচয়ের দ্বার খুলে দেবে বলেই ধারণা। শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে শিখছে না, তাই বলে তারা যে বাংলা ভাষা ভালোভাবে শিখছে তা মোটেই নয়। তাদের বাংলাজ্ঞানও অকিঞ্চিৎকর। উভয় ক্ষেত্রেই মূল কারণ অভিন্ন। সেটা হলো শিক্ষার্থীদের আগ্রহের অভাবের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। নিজের মাতৃভাষা যে ভালোভাবে জানে না তাকে কোনো বিবেচনাতেই শিক্ষিত বলা যাবে না। স্মরণীয় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জটি ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। সেটা আমরা করতে পারিনি। এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল যে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছি তা-ই নয়, শিক্ষাকে তিন ধারায় বিভক্ত করে দিয়ে শ্রেণিগত বিভাজনটি আরও গভীর করে তুলেছি।
বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সংস্থাটিকে বাংলা একাডেমিতে বিলীন করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষীণ একটি আশা ছিল যে, ওই বোর্ডের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে একাডেমি উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করবে। কাজটা শুরু হয়েছিল, থেমে গেছে। ইতিমধ্যে বাংলা একাডেমি যে অন্যায় কাজটা করেছে সেটা হলো প্রমিতকরণের নামে বাংলা বানানে অন্যায় হস্তক্ষেপ ঘটানো। প-িতরা যে কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারেন এই হস্তক্ষেপ তার এক ঐতিহাসিক দলিল।
শিক্ষা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে আমরা অন্তহীন অবকাশ সহজেই পাব। কিন্তু প্রতিকার কী? কেমন করে শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করতে পারব? সেটাই কিন্তু আসল সমস্যা। শিক্ষার মান কিছুতেই উঠবে না যদি না তা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারি। এক্ষেত্রে অন্তরায়টা কোথায়? স্পষ্টতই সেটা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। কাঠামোটি পুঁজিবাদী। আমাদের শাসক শ্রেণি আপাদমস্তক পুঁজিবাদে দীক্ষিত। পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত মুনাফা ছাড়া অন্যকিছু বোঝে না, এবং পুঁজিবাদ সব কিছুকে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত করে তবে ছাড়ে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে পুঁজিবাদী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এমন শিক্ষা দেয় যাতে সে আশপাশে দক্ষিণে বামে না তাকিয়ে কেবল নিজের লাভ-লোকসানের হিসাব কষতে শেখে। এটাই হয়ে দাঁড়ায় তার আরাধনা। এই ঘটনা নতুন নয়, এটা আগেও ছিল, কিন্তু এটাকে আমরা পাল্টাতে পারিনি। পাল্টাব কী, উল্টো এটাকে আরও বেশি পাকাপোক্ত করে তুলেছি। ইতিমধ্যে বাণিজ্য চলে এসেছে নর্দমার বিষাক্ত প্রবাহের মতো। এই প্রবাহ শিক্ষাকে সুস্থ থাকতে দেবে না।
পুঁজিবাদই হচ্ছে আসল ব্যাধি। এর বিরুদ্ধে লড়াই চাই। সে ক্ষেত্রে পাল্টা দীক্ষার প্রয়োজন হবে। ওই দীক্ষাটা সমাজতন্ত্রের। পুঁজিবাদের ভেতর আবদ্ধ থেকে পুঁজিবাদকে প্রতিহত কর, এটা সম্ভব নয়। দীক্ষার বদল চাই সর্বাগ্রে। তারপর আসবে অন্যসব বিবেচনা-পথ ও পাথেয়ের সন্ধান। সংস্কারে কুলাবে না। সংস্কার সংকটকে আরও গভীর করার মওকা তৈরি করে দেবে বলেই আশঙ্কা। এই সিদ্ধান্তটি তাই খুবই জরুরি যে, পুঁজিবাদী আদর্শ থেকে বের হয়ে আসা চাই এবং সে কাজটা না করতে পারলে যথার্থ অগ্রগতি বা উন্নতি কোনোটাই সম্ভব নয়। কারা নেবেন এই সিদ্ধান্ত? নেবেন দেশপ্রেমিক মানুষেরা। এদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরাই সর্বাগ্রগণ্য। সিদ্ধান্ত শিক্ষকরাও নেবেন। শিক্ষকদের সংগঠন আছে; সেসব সংগঠন পেশাগত দাবির জন্য লড়বেন তো অবশ্যই, সেই সঙ্গে শিক্ষাকে পুঁজিবাদের রাহু থেকে মুক্ত করার কথাও তাদের ভাবতে হবে, শিক্ষার স্বার্থে এবং নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় চরিতার্থতা লাভের স্বার্থেও।
দীক্ষা ছাড়া শিক্ষা নেই এবং যে দীক্ষায় রাষ্ট্র ও সমাজ এখন দীক্ষিত মানুষের মঙ্গলের জন্য এর চেয়ে বড় শত্রু এই মুহূর্তে আর দ্বিতীয়টি নেই। ভিন্ন এক আদর্শে দীক্ষা ভিন্ন পুঁজিবাদে আমাদের দীক্ষা থেকে মুক্তি নেই। দেশে মৌলবাদীদের তৎপরতা বাড়ছে, তারাও কিন্তু পুঁজিবাদীই; তারাও ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যই লড়ছে তবে তাদের আশা কেবল ইহজাগতিক নয় পারলৌকিক মুনাফাও। ইহলোকের সুখ স্বল্পকালীন, পারলৌকিক সুখ অনন্তকালের এভাবেই তারা সবকিছু দেখে। পুঁজিবাদীরা ইহজাগতিক, তাদের তৎপরতায় মানুষ শোষিত হচ্ছে এবং আমাদের নদী-নালা, অর্থনীতি ও মানবিক মূল্যবোধগুলো যেমনি, তেমনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও ভয়ংকর বিপদের মধ্যে আছে। প্লেটো-কথিত সেই বিখ্যাত গুহার ভেতর আটকা পড়ে থাকলে চলবে না, উন্মুক্ত সূর্যালোকে বেরিয়ে আসতে হবে।
লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়